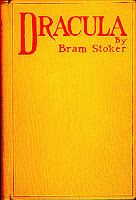সবার আগে কোন ট্রেন ছাড়বে ভাই? কাউন্টারে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো তুহিন। আপনি যাবেন কোথায়? ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন কাউন্টারম্যান।এখন যে ট্রেন ছাড়বে সে ট্রেনেরই টিকেট কাটবো।তা বুঝলাম কিন্তু কোথায় গিয়ে নামবেন?ট্রেন কোন রোডে যাবে তা জানার পর গন্তব্য ঠিক করবো।মাথা খারাপ নাকি!আমি একটু দুরে দাঁড়িয়ে। তবুও ওদের আলাপ আমার কানে আসছে সাউন্ড সিস্টেমের কল্যাণে। এই সাউন্ড সিস্টেম কমলাপুর স্টেশনের নতুন সংযোজন।
এখন আর কাউন্টারম্যানের সাথে গোপন চুক্তি করার সুযোগ নেই কারো। যে কেউ ওখানে গিয়ে কথা বললেই গম গম করে ওঠে সাউন্ডবক্স। সাউন্ডবক্সে কাউন্টারম্যানের ফ্যঁসফ্যঁসে গলা আর তুহিনের অধৈর্য্য ও বিব্রত কণ্ঠ শুনে আমিও এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোককে যতই বোঝাচ্ছি আমরা সত্যি সত্যিই গন্তব্য ঠিক করিনি, তিনি ততই ভাবছেন তার ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠের করণে আমরা তার সাথে মজা নিচ্ছি। বেশি বেশি কথা বলিয়ে যাত্রীদের কাছে তাকে হাসির পাত্র বানানোর চেষ্টা করছি।একবার যদি কারো এমন ধারণা হয়ে যায়, চেষ্টা করেও তার থেকে আন্তরিকতা পাওয়া যায় না। আমরাও পেলাম না।
অপমানে চোখ মুখ লাল করে তিনি আমাদের সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন। ব্যস্ততার ভান করে সহজ হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনো তার শুকনো শরীর ছিপছিপে রোবটের মতো টান টান হয়েই রইলো।আমরা তাকে আর বিব্রত করতে চাইলাম না। সরাসরি প্লাটফরমে অবৈধ অনুপ্রবেশ করলাম নিশিদলের দুই সদস্য।ঘটনাটা ঘটেছিলো গত ২৩ জুলাই। ১৩ই রমজান। কথা ছিলো রমজান মাসে কোনো ট্রিপে যাবো না। কিন্তু হঠাৎই উতলা হয়ে উঠলো তুহিন। দুপুরের দিকে ফোন দিয়ে বললো আজই একটা ট্রিপের ব্যবস্থা করতে। আমি সাময়িক আপত্তি করলাম অন্য সদস্যদের কথা ভেবে। বিশেষ করে রোমনের পক্ষে বিনা নোটিশে সময় বের করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তুহিনের ভেতরটা নাকি ভীষণরকম আনচান করছে। একটা নিশি ট্রিপে না যাওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে স্থির হওয়া সম্ভব নয়। কী আর করা অবশেষে দুইজনই রওয়ানা হয়ে গেলাম।প্লাটফরমে দাঁড়ানো নোয়াখালী এক্সপ্রেস। কয়েকটা মাত্র কামরা। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সময়জ্ঞান বলতে কিচ্ছু নেই ওটার। এর আরো সত্যতা মিললো বয়স্ক এক যাত্রীর কথায়। ভদ্রলোক যাবেন আশুগঞ্জ।
তিনি জানালেন সেখানে পৌঁছতে সকাল গড়াতে পারে। তখন সময় মাত্র আটটা বেজে ৩৫ মিনিট। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এর গতি কচ্ছপের চেয়ে খুব একটা বেশি নয়। আশুগঞ্জ যেতে হলে সারারাত ট্রেনেই কাটাতে হবে। সেই মুহূর্তে অন্তত এটা আমরা চাইনি। কাজেই কাছাকাছি কোনো স্টেশনে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়?দ্বারস্থ হলাম কর্তব্যরত এক পুলিশের- আঙ্কেল টঙ্গীর পর এই ট্রেনটা কোথায় ধরবে?তিনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মিস্টি একটা হাসি দিলেন। তারপর কুশল জিজ্ঞেস করে বসলেন- আপনারা ভালো আছেন আঙ্কেল?ভ্যবাচেকা খেলাম আমরা। তাকালাম চেহারার দিকে। অন্ধকারের ভেতরও চাঁদের মতো গোলগাল মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।দেখ কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! এই পুলিশ কনস্টেবলতো আমাদের আগের ট্রিপেও ছিলেন। লালমনি এক্সপ্রেসে টাঙ্গাইল পর্যন্ত আমাদের দলটাকে দেখেশোনে রেখেছিলেন তিনিই। কনস্টেবল ভদ্রলোকের নাম ফিরোজ। দ্বিতীয়বারের মতো দেখা হওয়ায় তিনি আরো অন্তরঙ্গ হলেন আমাদের সাথে।
কেবল আঙ্কেল থেকে হয়ে গেলেন ফিরোজ আঙ্কেল।ফিরোজ আঙ্কেলের সাথে পরামর্শ করেই আমরা গন্তব্য ঠিক করলাম- ঘোড়াশাল। নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা সদর ঘেঁষেই এই রেলওয়ে স্টেশন। ট্রেনে বাড়ি (কিশোরগঞ্জ) যেতে হলে এই স্টেশন মাড়িয়েই যেতে হয়। তবে কখনো নামার সৌভাগ্য হয়নি।নোয়াখালী এক্সপ্রেস কমলাপুর ছাড়লো রাত নয়টা পাঁচ-এ। কয়েকটি খুঁচরা স্টেশনে ক্রসিংয়ের জন্য লম্বা বিরতি দেয়ায় ভেবেছিলাম ঘোড়াশাল পৌঁছতে মধ্যরাত গড়াবে। কিন্তু না। মাত্র এক ঘন্টা ৪৫ মিনিট পরই আমরা পা রাখতে পারলাম ঘোড়াশাল প্লাটফরমে।শীতলক্ষ্যা সেতু পার হয়েই পুরনো ও শান্ত স্টেশন ঘোড়াশাল। ছোটখাট হলেও আভিজাত্যের ভাব আছে। দ্বিতল এই স্টেশনটির নিচতলা সমতল থেকে একটু ওপরে। আর উঁচু রেললাইন সমান্তরাল বয়ে গেছে প্লাটফরমের দ্বিতীয়তলা বরাবর।
এর গঠনটাও একটু ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় তলার প্লাটফরম থেকে তিনটি বড় বড় ধাপ নেমে এসেছে রেল লাইনে, যেখানটায় ট্রেন থামে। আর পুরো স্টেশনটি দাঁড়িয়ে আছে লাল ইটের দেহ নিয়ে। কোথাও কোথাও পুরনো টেরাকোটার গাঁথুনিও আছে। দেয়ালের এখানে সেখানে শিকড় মেলে আঁকড়ে আছে ছোট ছোট বটগাছ, পরগাছা। দূর থেকে দেখলেই গা ছমছম করে।আমাদেরও গা শিউরে উঠলো। ভয়ে নয়, ট্রেন থেকে নামার পরই কয়েকটি মোটাদাগের বৃষ্টির ফোটা বেয়াড়াভাবে আছরে পড়লো গায়ে। শরীরজুড়ে শিহরণ উঠলো। বাহ, চমৎকার বৃষ্টি। টিপ টিপ ঝড়ছে। আমরা প্রফুল্ল মনে ধীরেসুস্থে প্লাটফরমের তিনটি ধাপ ভাঙলাম। তারপর চোখ ঘুরালাম চারদিকে। নোয়াখালী এক্সপ্রেস থেকে নামা অন্য যাত্রীরা ততক্ষণে ত্রস্ত পায়ে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। রাত গভীর হওয়ার আগেই ওদের পৌঁছাতে হবে।
আমাদের কোনো তাড়া নেই। একটি রাতের জন্য এই স্টেশনই আমাদের বাড়ি। এটাই আমাদের আশ্রয়।আশ্রয়টাকে পাকাপোক্ত করার জন্য কয়েকচক্কর ঘুরলাম প্লাটফরমে। ভাবটা এমন যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছি যে, আজকের রাতটা আমরা স্টেশনেই কাটাবো। কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো। কিন্তু কেউ কোনো আপত্তি নিয়ে এলো না। কেবল কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে থাকলো। কেউ কেউ চিৎ হয়ে কাত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। স্টেশনের দুই দিকে দু’টো দলকে দেখলাম আড্ডা দিচ্ছে, বিড়ি ফুঁকছে। প্রতিটি দলে ছয়-সাতজন করে হবে। সবার পরনেই লুঙ্গি। কারো মাথায় গামছা বাঁধা।আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারলাম, এরা হলো রাতমানব। রাতে বিচরণ করে। রাতই এদের অন্ন যোগায়। রাত যত গভীর হয় এদের উপার্জনের পথও তত প্রশস্ত হয়।রাতমানবের আরো একটি দল পেলাম প্লাটফরমের নিচতলায় নামার পথে। সিঁড়ির বাঁকটাতে বসে ষোল কটি খেলছে। একবারের জন্য মুখ তুলে আমাদের দেখলো। তারপর আবার খেলায় মনযোগ দিলো। আমরা নেমে এলাম নিচতলায়। নিচতলা থেকে আরো একটু সিঁড়িপথ পাড়ি দিয়ে সমতল। অর্থাৎ স্টেশন রোড। স্টেশন রোডে পা রাখতেই চোখে পড়লো ঘোড়াশালের ঘোড়া।
সাদা ধবধবে এই ঘোড়ার মূর্তিটির ওপর আলো ঠিকড়ে পড়ছে। রাতের কালোতে আলোকিত ঘোড়াটি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠলো। সাদা পোশাকের সওয়ারি নিয়ে ছুটছে ওটা। দেখে মনে হলো আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট বিশ্বজয়ে বেরিয়েছেন তার প্রিয় ঘোড়া বুচিফালুসে সওয়ার হয়ে। সামনের ক্ষুর কুণ্ডলি পাকিয়ে লাফিয়ে নিজেকে শূন্যে ছুঁড়ে মারছে ঘোড়াটি। দুলকি চালে ক্ষিপ্র গতিতে ওটা ভেদ করতে চাচ্ছে অন্ধকারের চাদর।ক্ষিপ্র হয়ে ওঠলাম আমরাও। আমাদের এই ক্ষিপ্রতা খাওয়ার জন্য। গত ট্রিপে খাওয়া নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। তাই এবার এই বিষয়ে সচেতন রইলাম। ঘোড়াশাল চত্বরেই পেয়ে গেলাম ভাতের হোটেল। মুহূর্ত দেরি না করে ঢুকে গেলাম ঝুঁপড়িতে। ভাঙ্গা একটি দেউড়ি তোলা। সামনের দিকে লম্বা টেবিলে রান্নাকরা তরকারি সাজানো। পেছনে দুইটি টেবিলে চারটি করে আটটি চেয়ার পাতা। আমারা কোনার চেয়ারটি দখল করে বসলাম। প্রথমেই হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে নিলাম সেহরির সময় খাবার পাওয়া যাবে কি না।
তিনি অমায়িকভাবে বললেন- এমনিতে খোলা রাখি না, কিন্তু আপনেরা কি সেহরি খাইবেন?হ্যাঁ।তাইলে আইসা পইরেন, খাবার রাখুমনে। হোটেলওয়ালার নাম লিটন। কি কারণে যেন আমরা তার কাছ থেকে আলগা খাতির পেয়েছি। হাত ধুয়ে বসতে না বসতেই টেবিলে চলে এলো ধুয়াওঠা গরম ভাত। কয়েক মিনিটের মাঝে গরুর মাংস আর ইলিশ মাছের কড়া ভাজা। এমন জম্পেশ দুটো আইটেমের সাথে কি পেঁয়াজ কুচি আর কাচামরিচ ছাড়া চলে? মুখ ফুটে বলতে না বলতেই চলে এলো ও দুটো অনুষঙ্গও। ব্যস খেয়ে দেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আমরা এগিয়ে গেলাম শীতলক্ষ্যার দিকে। ঘড়িতে সময় তখন ১১টা বেজে ২০ মিনিট। টিপ টিপ বৃষ্টিটা তখনো রয়ে গেছে। বেয়াড়া ফোটায় গা ভিজছে না, আবার একেবারে হালকাও মনে হচ্ছে না। আমরা বসলাম শীতলক্ষ্যার জল ঘেঁষে বড় একটি পাটাতনের ওপর। সেতুতে বসানোর জন্য নির্মিত এই পাটাতনগুলোর একেকটি আয়তনে প্রায় বড়সর বাসের মতো। হাতের বাম দিকে সড়ক সেতু। আর ডানে রেল সেতু। আমরা মাঝখানে বসে একবার সড়ক সেতুর গাড়ির হেডলাইটগুলোর আনাগোনা দেখছি, আবার তাকাচ্ছি রেল সেতুর দিকে।
মাঝ নদীতে ভাসছে কার্গো।থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টির টিপটিপানিটা বেশ ধৈর্য্য সহকারে অব্যহত রয়েছে। শীতলক্ষ্যার জল ঘেঁষে এমন একটি জায়গায় নির্বিঘ্নে তা কল্পনায়ও ছিলো না। নেই কোনো নেশাখোর বা ছিনতাইকারির উৎপাত। বলা যায় বিনা উতপাতে আমরা একরকম অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। এভাবে শীতলক্ষ্যাকে সামনে নিয়ে বসে থাকলে রাতটাই মাটি হয়ে যাবে। মিনিট তিরিশেক পর ওঠে দাঁড়ালাম। গন্তব্য এলোপাতাড়ি। সত্যি সত্যিই এলোপাতাড়ি ঘোড়াফেরা করলাম স্টেশন রোড ধরে। তারপর আবার গো ব্যাক টু হোম। অর্থাৎ আমাদের একরাতের বাড়ি স্টেশনে।হতাশ হলাম। স্টেশনের চিত্রটা তেমন পাল্টায়নি। সেই আগের মতোই, কোনো বিপদও এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়নি। কেন? এই রাত মানবরা কী আমাদের আত্মীয় হয়ে গেলো!মোটেই না। এমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই। এরা হয়তো সুযোগের অপেক্ষায়। আমাদের বোঝার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, এখানে কতক্ষণ থাকবো ইত্যাদি। বুঝতে পারলাম আমরা দু’জনকে ঘিরে রাতমানবদের ভেতর মোটামোটি শোরগোল পড়ে গেলো। তবে এগিয়ে আসছে না কেউ।
কিন্তু একজনকে দেখে এগিয়ে যেতে হলো আমাদেরই। প্রথমে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলাম। প্লাটফরমের ছাউনির ঠিক শেষ দিকে একটি পিলারে হেলান দিয়ে আছে লোকটা। চোখে চশমা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে প্যন্ট আর ছাই রঙের শার্ট। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একেবারে সমাজছাড়া লোক। কোনো জটলায় নেই, সেই অন্ধকার কোনায় হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। আর পিলারে হেলান দিয়ে উদাস হয়ে কী যেনো ভাবছে। দূরের বৈদ্যুতিক বাতির আলো তার চশমায় ঠিকড়ে আবার ফেরত আসছে। রাত একটায় রেলস্টেশনে এমন একজন ভদ্রলোকের এভাবে বসে থাকাটাই অস্বাভাবিক। ওই রাতমানবদের কাছে আমাদের গতিবিধি অস্বাভাবিক। আবার আমাদের কাছে অস্বাভাবিক এই উদাসি লোকটা। যদিও তার আচরণ নিশিদলের থিম এর সাথে মানানসই, তবুও সন্দেহ হলো। আমরা না হয় খামোখাই বিপদ মাথায় নিতে পছন্দ করি। তাই বলে সব লোক কী আর আমাদের মতো? সন্দেহ আরো ঘনিভ’ত হলো রাতমানবেরা আমাদেরকে নিয়ে যতটা মাথা ঘামাচ্ছে এই লোককে তেমন পাত্তাই দিচ্ছে না। তাহলে কে এই লোক?বাড়ি থেকে অভিমান করে বেরিয়েছে?ফেরারি আসামি? বড় কোনো সন্ত্রাসী? চোরাকারবারি? ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান যাত্রী? এটা তো হবেই না। নিখাদ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করলে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকার কথা নয়।
সাধারণত বিপদগ্রস্ত বা রাতের অপেক্ষমান যাত্রীরা স্টেশনের সবচেয়ে আলোকিত ও নিরাপদ যায়গাটিই বেছে নেয়। কিন্তু এই ভদ্রলোক তার সাথে থাকা পাটের ব্যগটিতে কনুইয়ের ভর রেখে মাথা ছেড়ে দিয়েছে পিলারে। পায়ের স্যান্ডেলজোড়া এলোমেলো ছড়িয়ে মাঝে মাঝে হাই তুলছে আর এপাশ ওপাশ করছে। এই রহস্যমানবের আরাম দেখে খুব লোভ হলো আমাদের। তার পরিচয় যাই হয়ে থাকুক, মনে হলো জীবনটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে। সাধারণত উত্তরবঙ্গের নিষিদ্ধঘোষিত বাম বিপ্লবী নেতারা এই ধরনের হয়ে থাকে। একটা আদর্শকে লালন করে এর জন্য জীবন উৎসর্গ করে। সমাজ-সংসার বলতে কিচ্ছু থাকে না এদের। পুরো জীবনটাই ফেরারি কাটাতে হয়।আমরা এগিয়ে গেলাম তার দিকে। ভদ্রলোকের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সরাসরি চোখে চোখে চাইলাম, তারপরও না। আশপাশের অনুষঙ্গগুলোকে কোনোরকম তোয়াক্কা না করে এত্তো স্বাভাবিক থাকা যায় কি করে!অবাক হলাম আমরা। এ তো দেখছি যেনোতেনো লোক নয়, গভীর জলের মাছ। আরো একটু সময় নিতে চাইলাম। তুহিন চলে গেলো লোকটাকে পাশ কাটিয়ে। আমিও রেল লাইন ধরে তার পিছু পিছু। বলে রাখা ভালো বৃষ্টির ধারায় তখনো বিরাম পরেনি। আমরা এই রহস্যমানবকে পাশ কাটিয়ে মোটামোটি অনেকটা চলে এসেছি রেলসেতুর দিকে। ঢুকে গেছি অন্ধকারে।
রেললাইনের ঢাল বেয়ে ঘন ঝোঁপ। ধুতরার কাঁটা। আবার কী যেন একটা বন্য ফুলের গন্ধও আসছে নাকে। গোটা পরিবেশটাই মাতাল মাতাল। বাতাসের একেকটি ঝাপটায় হুড়মুড় করে ডালে ডাল বাড়ি খাচ্ছে বড় গাছগুলোয়। বিরহি হয়ে ওঠলো মন। শুন্য মনে হলো নিজেদের। এখানে দুইজন, তবুও মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে আমি একা। খুব ইচ্ছে হলো কারো হাতে মন সঁপে দিতে। মনের কথাটা খুলে বলতে। ভেজা বাতাসে ছেড়ে দিলাম গলা – ‘এমনো দিনে তারে বলা যায়/ এমনো ঘন ঘোর বরিষায়/ এমনো মেঘস্বরে/ বাদলো ঝড়ো ঝড়ে/ তপনহীন ঘন তমশায়’গান গাইলাম দু’জনই। আপ্লুত হয়ে গাইলাম। তারপর হৃদয় তোলপাড় করে তুললাম আরো একটি সুর- ‘মায়াবনো বিহারনী হরিনী/ গহনো স্বপনো সঞ্চারিনী/ কেনো তারে ধরিবারে করিপণ/অকারণ/ থাক থাক নিজোমনে দূরেতে/ আমি শুধু বাঁশরিরো সুরেতে/ পরশো করিবো ওর প্রাণোমন/অকারণ’সাধারণত কবিগুরুর এই গানটা ভঁজলেই একটা ঘোর তৈরি হয় আমার। এবারও হলো। কিন্তু এই ঘোওে ফাল হয়ে ঢুকলো বৃষ্টি। স্বাভাবিক ছন্দের চেয়ে একটু বেশি ঘন ঘনই ফোঁটা ঝড়তে শুরু করলো আকাশ থেকে। সুতরাং আবার স্টেশনের ছাউনির ভেতর। আবার সেই রহস্যমানব।লোকটার কানে সম্ভবত আমাদের হেঁড়ে গলার সুর চলে এসেছিলো। এবার সে নিজ থেকেই কৌতুহল নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। যতটুকু বুঝলাম আমাদের গতিবিধিও তার কাছে পরিষ্কার নয়। আমরা মনে মনে খুশিই হলাম। এবার তাহলে আলাপ জমানো যাবে। যেচে গিয়ে কথা বলতে চাইলাম। ‘ভাই কী ঢাকায় যাবেন?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।কোনো জবাব নেই। রহস্যমানব একবারের জন্যও চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইলো আমার দিকে। আমি তার দিকে।‘বলি, ভাই কী ঢাকার যাত্রী নাকি?’এবার দুইমন ওজনের ভারি গলায় জবাব দিলো ‘হুম’।
ভারে কুঁজো হয়ে এলো আমার গলা। এই ‘হুম’ বলার ভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের সাথে কথা বলতে সে আগ্রহী নয়। তবুও শেষ চেষ্টাটা করলো তুহিন ‘ট্রেন কয়টায় আসবে?’আবারো চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো। সেকেন্ড দশেক হবে। তারপর আমাদেরকে একরকম অপমান করেই চোখ ঘুরিয়ে নিলো। শরীরটা লম্বা করে টানা দিয়ে দুই হাতে পেছনের পিলারটা শক্ত করে আঁকড়ে হারিয়ে গেলো উদাসপুরে।এই অপমান গায়ে মাখলাম না আমরা। তবে নতুন করে আবার অপমানিতও হতে চাইলাম না। আপাদত গভীর জলের এই মাছটাকে জলে খেলতে দেয়াই ভালো। আমরা বরং একটু সমতলটা ঘুরে আসি।ঘড়ির কাঁটা তখন একটা পেরিয়ে। বসে আছি বাবুল চাচার দোকানে। ঠিক যে দোকানটায় রাতের খাবার খেয়েছিলাম এর পাশের দোকানটিই তার। খোলা থাকে সারারাত। এই দোকানটাই তার সংসার। একা থাকেন। আমাদের সাথে কথা বলতে বলতে তিনি নিজের জন্য কৈ মাছ কাটছেন। রান্না করবেন এবং সেহরি খেয়ে রোজার নিয়ত করবেন। কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা ও মোটাসোটা গড়নের এই বাবুল চাচার বাড়ি নোয়াখালী।নোয়াখালী রেখে ঘোড়াশালে কেন ব্যবসা করতে এলেন?
পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি ‘নোয়াখালীর লোক বাংলাদেশের কোন যায়গায় নাই? চান্দে গেলেও পাওয়া যাইবো।’আমরা হাসলাম। বাবুল চাচার দোকানের বেঞ্চিতে বসে ফুড়–ৎ ফাড়–ৎ শব্দ তুলে দুই কাপ রঙ চা খেলাম। কলার কাঁদি থেকে সাবার করলাম দুইটি শবরি কলা। বাবুল চাচা বেশ অমায়িক ও পরোপকারি লোক। আমাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন রাতটা কাটাতে হলে কোথায় বসতে হবে, কোন পথে যেতে মানা। আর কোথায় কোথায় ঠেক দেয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরাও সম্মানের সাথে তার পরামর্শগুলো শীরোধার্য্য করলাম। কেবল দ্বিতীয়বারের মতো শীতলক্ষ্যার পারে গিয়ে তার বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন করে ফেললাম। বাবুল চাচা বলেছিলেন তার দোকানের চৌহদ্দিতেই যেন থাকি। খুব হাঁটতে ইচ্ছে করলে একটা সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন। আমাদের নিয়ে তাঁর এ শঙ্কাগুলো মোটেও অমূলক ছিলো না। দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকা অবস্থায়ই এক লোক আমাদেরকে জোটমিলের দিকে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করছিলো। বাবুল চাচা ইশারা ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছিলেন সেদিকে যাওয়া ঠিক হবে না। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে লোকটা চলে যাওয়ার পর তিনি জানালেন, এই লোক প্রতি রাতেই যাত্রীদের ঠেক দেয়। ছুরি মারে।
কুপিয়ে জখম করে।এসব ঝুট-ঝামেলা মোকাবেলার জন্য আমরা দুইজন মোটেও যথেস্ট নই। তাই খুব ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও বাবুল চাচার রেড এলার্ট জারি করা প্রতিটি অলিগলিতে অনুপ্রবেশ করতে পারিনি। নিশিদলের অপ্রতুল সদস্য নিয়ে তা সম্ভবও নয়। তবুও একটা না একটা এলার্ট তো ভাঙতেই হবে।পা চালালাম শীতলক্ষ্যাকে বামে রেখে পলাশের দিকে চলে যাওয়া পথ ধরে। মোটামোটি প্রশস্ত পথ। বিরতি দিয়ে দিয়ে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে ‘প্রাণ’ কোম্পানীর গাড়ি। নরসিংদী জেলার অন্যতম শিল্প এলাকা এই ঘোড়াশাল। এখানে বাংলাদেশের বড় বড় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানেরই কারখানা রয়েছে। রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা। এসব কারখানাগুলো একদিকে যেমন শীতলক্ষ্যার টুটি চেপে ধরেছে, অন্যদিকে এ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানও করছে।আমরা হাঁটছি শীতলক্ষ্যার পাশ দিয়ে। দুই কুলে যান্ত্রিক কারখানা থাকলেও নদী তো নদীই। জলের আলাদা একটি মাত্রা আছে। সেই মাত্রাটাই উপভোগ করছি আমরা।
যদিও সড়ক থেকে জলের অস্তিত্ব ততটা দৃশ্যমান নয়, তবুও জলঘেঁষে বেড়ে ওঠা ফসল, ঝোঁপগুলো আমাদের ভেঙ্গেচুঁড়ে একাকার করে দিলো। ভর নিশিতে ঝিঁঝিঁর ডাকে হৃদয়টা হু হু করে ওঠলো। ইচ্ছে হলো পৃথিবীটা ওলট পালট করে দিই।কিন্তু না, ওলট পালট আর করা হলো না। যতটা নিশ্চিন্তে হাঁটছিলাম, ঠিক ততটা নিরাপদ আমরা নই। আমাদেরকে পেছন থেকে অনুসরণ করছে এক রাতমানব। বুঝতে পারলাম আশপাশে আরো আছে। আমি ফিরে যেতে চাইলাম। তুহিন সাহস দেখালো। নাচতে যখন নেমেছি, তো আর ঘোমটা দিয়ে কী লাভ?চমৎকার। বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। এই ফোলানো বুকই সম্ভবত রাতমানবের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো আমাদের। ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, আমরা কারা! ওরা আমাদের নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করে, গবেষণা করে। তারপর আমাদের অদ্ভ’ত আচরণ দেখে ভড়কে যায়।এভাবে রাত মানবদের ভড়কে দিতে দিতে মাত্র আধ ঘন্টার পথ হেঁটে আমরা চলে এলাম পলাশ। পথে পাড়ি দিয়েছি কয়েকটা কবরস্থান, শ্মশানঘাট। রাত তখন একটা বেজে ছয়ত্রিশ মিনিট। আমাদের হাতের বাম দিকে ‘প্রাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক’ এর সাত নাম্বার গেট। আর ডানে ‘পলাশ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা’।
আমরা হাঁটছি সামনে। উদ্দেশ্য এই কারখানার শেষটা ছুঁয়ে যাবো। সম্ভবত আধা কিলোমিটার হাঁটতে হলো। তারপর একে একে সাতটা গেট পেরিয়ে দেখতে পেলাম কারখানার এক নাম্বার গেট। বিশাল এলাকা নিয়ে এই কারখানায় কাজ করে স্থানীয় ও ভাসমান অনেক শ্রমিক। পুরো কারখানা এলাকায়ই দেখলাম রাতপ্রহরীদের ব্যপক আনাগোনা। ধারালো বর্ষার ফলা তোলে ওরা হাঁটছে। আমাদের প্রতি কোনো কৌতুহল দেখালো না। কারখানার বিপরীতদিকে দেখলাম অসংখ্য টিনসেডে শ্রমিকরা সাইকেল আমানত রেখে কাজ করতে গেছে। ওগুলোও পাহারা দিচ্ছে রাতপ্রহরীরা। একটি নির্জন মুহূর্ত কাটিয়ে এখানে এসে মানুষের সমাগম পেলাম। ইচ্ছে হলো এই সমাগমের ভেতর বসে চা খাওয়ার। যেই এমন ইচ্ছে করলাম অমনি টিপটিপানি বৃষ্টিটা আবার ফিরে এলো। ঝরতে শুরু করলো আগের ধারাবাহিকতায়। এটাকে খুব একটা তোয়াক্কা করলাম না। স্টেশনে নামার পর থেকে এই বৃষ্টিকে সাথে নিয়েই আছি আমরা। মাঝখানে কিছু সময় বিরতি দিয়েছিলো এই যা। কিন্তু যেই না গিয়ে চা দোকানের বেঞ্চিতে বসলাম, অমনি শুরু হলো ঝুম বৃষ্টি, এলোমেলো বাতাস। বৃষ্টির ছাঁট এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে।
দোকানী বললো বেঞ্চিটা একটু ভেতরের দিকে ঠেলে বসতে। তারপর মনযোগ দিলো টেলিভিশনে। দোকানীসহ আরো তিনচারজন ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে ’ফক্স মুভিস’ চ্যানেলে। রঙ্গমঞ্চে ড্যন্স চলছে। কোনো বিনোদিনী নয়, কয়েকজন পুরুষ বিনোদক কায়দা কসরত করে নেচে আনন্দ দিচ্ছে উন্মত্ত নারীদের। মুভির নাম ‘ম্যাজিক মাইক’ সম্ভবত এখানে উল্টো দেশের মতো উল্টো নিয়ম কানুন চিত্রায়িত হয়েছে।মুষলধারে বৃষ্টির জন্য মিনিট পঁচিশেক বসে থাকতে হলো দোকানেই। এর মধ্যে দু’জন দুই কাপ চাও গিলে ফেলেছি। অবশেষে সোয়া দুইটার দিকে বৃষ্টিটা টুটে এলে আমরা উঠলাম। এবার ফিরতে হবে।দোকান থেকে কয়েক কদম এগিয়েই দেখলাম একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশাওয়ালা পঞ্চাশ টাকার নিচে যাবেনই না। আর আমরা চল্লিশ থেকে এক টাকাও বেশি দিতে রাজি না। হেঁটে যখন আসতে পেরেছি, যেতেও পারবো। পা বাড়ালাম দুই নিশিকুটুম্ব।কিন্তু পেছন থেকে ডাকলো রিকশাওয়ালা। অর্থাৎ চল্লিশেই রাজি। আমরাও ঝটপট ওঠে বসলাম। তিন চাকা ঘুরলো ঘোড়াশাল রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। জনসমাগমের আলোর ঝলকানি ছেড়ে প্রবেশ করছি নিরব অন্ধকারের ভেতর।
রাতপ্রহরীরাও অব্যক্ত বিদায় জানালো আমাদের। একজনের মোবাইল ফোন থেকে ভেসে এলো হৃদয় ছেঁড়া গান- ‘আমার হৃদয়ে কে মারলো প্রেমের ছুরিরে’ আমরা আনমনা হলাম ।কিন্তু একরকম জোর করেই ভাবের জগত থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনলেন রিকশাওয়ালা। প্রথমে কিছু একটা বললেন, শুনতে পেলাম না। তারপর গলার আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- আপনাগো আগেদিয়া কয়েকটা পোলা আছিলো খেয়াল করছিলেন?কখন?চা ইস্টল থেইকা বাইরানির সময়?অনেকেইতো ছিলো।না, কয়েকটা পোলা আপনেগো টার্গেট করছিলো।টার্গেট করছিলো!হো, আপনেরা হাঁইটা একটু আন্ধাইরে গেলেই হ্যরা ঠেক দেওয়ার ফিকির করছিলো।রিকশাওয়ালার কথা শুনে আমরা হাসলাম। যেন এসব আমাদের কাছে ব্যপারই না। তবে চেষ্টা করেও হাসিটা প্রাণবন্ত করতে পারলাম না। কিছুটা শুকনো শুকনোভাব রয়েই গেলো।পোলাপাইনগুলো এই এলাকারই। মেলাক্ষণ ধইরা আপনেগো ফলো করতাছে। ওগো সব সব আলাপ আমার কানেও আইতাছে। যেই চা ইস্টল থেইকা বাইরাইলেন, হেরাও আপনেগো আগে আগে বাইরাইয়া গেলো। তাই নাকি!
এমনিতে রাইতের বেলায় পঞ্চাশ টেকার কমে ইস্টিশনে যাই না। কিন্তু পোলাপাইনগুলোর মতিগতিক খারাপ দেইখা আপনেগোরে ডাক দিয়া লয়া লইলাম।ভালো করেছেন চাচা।চিন্তা করলাম দশ টেকা আর কি ঘটনা। আপনেগো নিরাপদে ইস্টিশনে দিয়া আইতে পারলে মনডায় শান্তি পামু।কিন্তু রিকশায় ওঠার পরওতো ওরা আমাদের আটকাতে পারতো।আমার প্যসেঞ্জাররে আটকাইলে থাবড়াইয়া দাঁত ফালায়া দিমু না।ওরা কি আপনাকে মান্য করে?না, তা করে না। আপনেগোরে নামইয়া যাওয়ার পর ওরা আমার লগে ওনাপেনা করবো। ওইগোলার চৌদ্দগোষ্ঠী আমি চিনি। অপকর্ম কইরা একবার জেলে যায়, আবার হ্যাগো বাপ-মায় গিয়া ছাড়াইয়া আনে।বাপ-মায়ের কথায় পুলিশ ছেড়ে দেয়?ওইগুলো একেকটা নেতা-পেতার পোলাপান। বাপগুলার রোজগারের রাস্তাই তো হালাল না। চান্দা-ধান্দা কইরা পেট চালায়। হারাম রোজগার করলে পোলাপান মানুষ অয়না। ভালা মানুষের সন্তান খারাপ অয় খুব কম।
ওইগুলারে হাজতে ধইরা নিলে যদি ছাড়াইয়া না আনতো তাইলে দেখতেন জনমের শিক্ষা অইয়া যাইতো।আমরা মাথা নেড়ে সমর্থন করলাম। মুখে উচ্চারণ করলাম ‘হুম’।আরে, আমার একটা পোলা কিছুদিন ওইগোলার সাথে মিশতো। একদিন হ্যার চাচায় ধইরা এমন ঠ্যাঙ্গানি দিছে। অহন সিধা অইয়া গেছে। মাথা নিচা কইরা ফ্যটকরিতে (ফ্যক্টরিতে) কামে যায় আর আইয়ে।রিকশাওয়ালা চাচার নাম হোসেন মিয়া। মধ্য বয়স্ক, সুঠাম দেহ। থুতনিতে কাঁচাপাকা দাড়ি। রাত পৌনে তিনটার দিকে হোসেন চাচা আমাদের নামিয়ে দিলেন স্টেশনের পেছনের দিকটায় ঘোড়াশাল চত্বরে। আমাদের প্রতি তার আন্তরিকতার কারণে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশিই ধরিয়ে দিলাম আমরা। তাই তিনি খুশি হয়ে পই পই করে সাবধান করে দিলেন আমাদের- ট্রেন আসার আগে যেন আমরা প্লাটফরমে না যাই। ঘোড়াশাল স্টেশন এলাকাটা খুবই খারাপ। রাতের বেলায় ঠেকবাজরা যারে তারে খুর দিয়া পোছায়।সেই মুহুর্তের জন্য হোসেন চাচাকে মান্য করে আমরা সেঁধিয়ে গেলাম ভাতের হোটেলে সেহরি খাওয়ার জন্য। লিটন মিয়াকে দেখলাম একনিষ্ঠ মনে টেলিভিশনে বাংলা সিনেমা দেখছে।
জানালো আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলো সে। হাত ধুয়ে বসার পরই ঝটপট খাবার চলে এলো সামনে। টিভিতে তখন চলছে এ্যকশন দৃশ্য- খলনায়কের এসাইন করা এক ডাইনি নায়িকা হাতে ছুরিু নিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটছে নায়কের কামরার দিকে ‘আজ রাতেই ওকে শেষ করতে হবে’ কিন্তু না ধরা খেতে হলো তাকে। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় উদভ্রান্তের মতো ছুটার সময় ছুরিু হাতে নায়িকাকে দেখে ফেলেছে দাদিমা। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য পাগলের মতো আবোল তাবোল বকতে লাগলো ডাইনিটা। অভিনয় কাজে দিলো। কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করলো না নায়িকাকে। আদুরে গলায় চেঁচামেচি শুরু করলো দাদিমা- ‘আরে আরে ওতো দেখছি পাগল হয়ে গেছে। রাতদুপুরে ছুরি নিয়ে হাঁটে।’দৃশ্যের পরিবর্তন। পর্দায় অট্টহাসি নিয়ে আবির্ভূত হলো খলনায়ক কাবিলা।তারপরই বিজ্ঞাপন বিরতি- স্বামীকে বাধিত রাখতে চান? প্রেম ভালোবাসায় ব্যর্থ? মালিককে বশ করতে চান? লটারিতে বিজয়ী হতে চান? তাহলে আজই চলে আসুন এ দেশের শ্রেষ্ঠ জ্বীন সাধিকা, আধ্ম্যাতিক জগতের শিরমনি গুরু মা মরিয়ামের দরবারে।দীর্ঘ বিজ্ঞাপন চলতে চলতেই আমরা খাওয়া শেষ করলাম। লিটনের ভাতের দোকান বন্ধ হলো।
দেখা হলো নোয়াখালীর সেই বাবুল চাচার সাথে। তিনিও রিকশাওয়ালা হোসেন চাচার মতো আমাদেরকে এই মুহূর্তে স্টেশনে যেতে বারণ করলেন।কিন্তু সব বরণ কি আর সবসময় রাখা যায়? বাবুল চাচার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা ঠিকই চলে গেলাম স্টেশনে। রাতমানবদের অনেকেই তখন স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। উধাও হয়ে গেছে সেই রহস্যমানবও। স্টেশনটা আগের চেয়ে অনেকটা নেতিয়ে এসেছে। জাগতে শুরু করেছে ঘুমন্ত শ্রমিকেরা। আমরা মিনিট পাঁচেক পায়চারি করলাম। আবার নোয়াখালি এক্সপ্রেসেই ঢাকায় ফিরবো বলে ঠিক করলাম। ট্রেন আসার সঠিক সময় সাড়ে তিনটা। আমরা ধরে নিলাম সেটা আসতে আসতে সাড়ে চারটা কি পাঁচটা গড়াতে পারে। কিন্তু ভোর ছয়টায়ও দেখা মিললো না নোয়াখালী এক্সপ্রেসের।অবশেষে হতাশ হয়ে আমাদের ঢাকায় ফিরতে হয়েছিলো চার চাকার বাসে চড়ে। কিন্তু সাড়ে তিনটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত মাঝখানের এই আড়াই ঘন্টা কাটলো কিভাবে?সে আরেক ঘটনা।
ট্রেনের অপেক্ষায় ঝিমুনিতে টলতে টলতে স্টেশনের একটি ধাপে বসেছিলাম আমরা। একটু পর পর এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করে ট্রেনের খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করছিলাম। সেই সুবাদেই আলাপ জমেছিলো আমাদের বয়সি এক তরুনের সাথে। বাড়ি স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও। একেবারে রসিয়ে রসিয়ে আলাপ চলছিলো। জীবনের উত্থান-পতন, মন দেয়া নেয়াসহ অনেক বিষয়ই গড় গড় করে ঢালতে লাগলো সে। আমরাও ধৈর্য্যসহকারে শুনছি তার সকল তরল-গড়ল। সম্ভবত এ ধৈর্যের সুফল হিসাবেই আমাদের ওপর একটা আস্থাও তৈরি হয়ে যায় লোকটার। আর এই আস্থার ওপর ভর করেই এগুতে পেরেছি বাকিটাও।হাতে টর্চ নিয়ে সে অধৈর্য সময় পার করছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের এক যাত্রীর অপেক্ষায়।যাত্রী কী হয় আপনার?কিছু হয় না। আমারে চার লাখ ট্যকার মাল বুঝায়া দিয়া চইলা যাইবো।কপাল কুঁচকে এলো আমার। রহস্যের গন্ধ এসে ঠেকলো নাকে। এতো রাতে চার লাখ টাকার ’মাল’! পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম, কথা চালিয়ে যেতে হলে স্বাভাবিক থাকতে হবে। তার অলক্ষ্যেই কুঁচকানো কপাল আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলাম। প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়ে শূন্যে ঢিল ছুঁড়লাম- আপনার ওই লোক কি আখাউড়া থেকে আসছে?ঢিলটা যায়গামতোই পরলো। চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার- ভাইতো দেহি ম্যালা বুদ্ধিমান। আসল যায়গায় হাত মারছেন।
বলে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো একবার। আমি বিনয়ের সাথে হাসলাম। তুহিনের তখন ঘুমে ঢুলোঢুলো অবস্থা। আমাদের পাশে বসে থেকেও এদিকে খুব একটা মনযোগ নেই। তবে হয়তো আবছা আবছা বুঝতে পারছে ঘটনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্টেশন হলো চোরাচালানি আর মাদকব্যবসায়িদের স্বর্গরাজ্য। আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অবৈধ পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ওখানকার চোরাচালানিদের নেটওয়ার্ক অনেক শক্তিশালী। ওরা যে কোনো সময় স্টেশন ছাড়াও যে কোনো স্থানে ট্রেন থামিয়ে পণ্য লোড করার ক্ষমতা রাখে।এবার আরো ভরসা পেলো তরুণ। দূরে ঘুর ঘুর করতে থাকা আরেক সহযোগিকে ইশারায় ডাকলো। লুঙ্গি পরিহিত বিশ-বাইশ বছরের ওই ছেলাটাও পরম নিশ্চিন্তে আমার পাশে এসে বসলো। সম্ভবত আমার চোখের ভাষায় বুঝতে পেরেছে, আমি ওদের জন্য ক্ষতিকারক কোনো বস্তু নই।আমিও এবার ব্যপক উৎসাহ নিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম- এই চালানে কী কী ‘মাল’ আসছে?পিল। আর মসুরির ডিল।অর্থাৎ ইয়াবা আর ফেন্সিডিল। ওরা ইয়াবাকে সাঙ্কেতিক নামে ‘পিল’ বলে ডাকে। আর ফেন্সিডিলের পরিচিত নাম ‘ডাইল’
সে ছন্দ মিলিয়ে বলেছে ‘পিল, আর মসুরির ডিল।’ ভালো একটি অন্তমিল দিয়েছে।এর পরের দৃশ্যটা আরো আন্তরিকতাপূর্ণ। সে মাদকের পাইকারি ব্যবসায়ি। অবশ্য আশপাশের ভাই-বেরাদরদের খুঁচরাও সাপ্লাই দেয়। ওর এখান থেকে চালান যায় ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে। পারষ্পরিক সৌহার্দপূর্ণ আলাপে সে খোলামেলা ধারণা দিলো। ধারণা দিলো এই ব্যবসার শিরা-উপশিরা সম্পর্কে। জানালো এ পেশায় নামলে দ্রুতই লালে লাল হওয়া সম্ভব।অল্প সময়ে লাল হওয়ার একটা ইচ্ছা চাড়া দিয়ে উঠলো আমার। যদিও এই তরুণকে দেখে লালে লাল মনে হলো না। তবুও এগুলাম সরাসরি ব্যবসায়িক আলোচনায়- আমাকে একটা সুযোগ করে দিন না।খিক খিক করে হেসে উঠলো তরুণ। পাশে বসা সহযোগির পিঠে ঠাস করে একটা চাপড় বসালো- কীরে ব্যটা, তুই তো খালি খালি সন্দেহ করলি। কইছিলাম না এরা আমগো লাইনের লোক। রাইতের বেলায় ইস্টিশনে কী কেউ ধান্দা ছাড়া ঘুরে?বেচারা সহযোগির চেহারাটা দেখার মতো নিরীহ হয়ে উঠলো।
মিস্টি একটা হাসি দিয়ে আত্মসমর্পন করলো পেশাগত গুরুর কাছে।আমি আবারো হাসলাম। আরো ভরসা পেলো তরুন- আমি চেহারা দেইখাই লোক চিনি। আপনেরা গাড়ি থেইকা নামার পরই আমি ধরতে পারছি ব্যপারটা। তারপরেও নিশ্চিত হইবার লাইগ্যা অনেকক্ষণ ফলো করতে হইছে। খালি ইস্টিশনে না। ইস্টিশন থেইকা বাইর অইয়া কই কই গেছেন, কই খাইছেন সব কইয়া দিতে পারুম।সত্যিই সব পই পই করে বলে দিলো লোকটা। অবাক হলাম আমি। কিন্তু চেহারায় নির্বিকার রইলাম।এর পরের ঘটনা এগিয়ে গেলো নদীর রাতের মতো। অল্প সময়ে লালে লাল হওয়ার আকাঙ্খায় চোখ বড় বড় করে শিখলাম ব্যবসায়ের কৌশল। এই ব্যবসায় আদাজল খেয়ে নামবো বলে চ’ড়ান্ত সিদ্ধান্তও নিয়ে নিলাম। তারপর আমার সেলফোনে ওর নামে সেভ করলাম এগার ডিজিটের একটি নাম্বার। তবে ব্যবসায়িক বিবেচনায় সেই নাম ও নাম্বারের কোনোটাই এখানে উল্লেখ করতে পারছি না। কারণ এই লাইনে কাজ করতে হলে পারষ্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখাটা জরুরি।